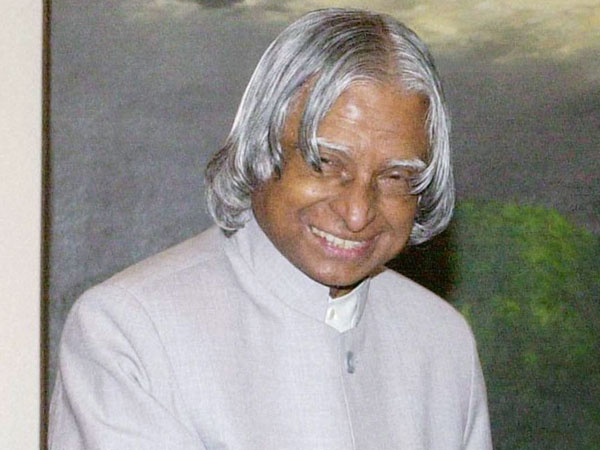বাঙালী কণ্ঠ ডেস্কঃ প্রায় এক দশক পর গত ১ ফেব্রুয়ারি পুনরায় মিয়ানমারের শাসনভার গ্রহণ করেছে দেশটির সেনাবাহিনী। গত বছরের নভেম্বরে নির্বাচন হওয়ার পর এ দিনটিতেই পার্লামেন্টের প্রথম অধিবেশন বসার কথা ছিল। তার আগেই সেনাবাহিনী নির্বাচিত সরকারকে হটিয়ে ক্ষমতা দখল করে নিল। গ্রেফতার করা হলো স্টেট কাউন্সেলর অং সান সু চি, প্রেসিডেন্ট উইন মিন্টসহ কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের শত শত নেতাকে। সু চির মন্ত্রিসভার ২৪ জন মন্ত্রীকে বরখাস্ত করা হয়েছে। দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোতে জোরদার সেনা টহল চলছে। গণমাধ্যম, এমনকি ইন্টারনেট যোগাযোগও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে
মিয়ানমারে যে এমনটি হতে যাচ্ছে তার পূর্বাভাস বিশ্ব গণমাধ্যম আগেই দিয়েছিল। এ আশঙ্কার কথা সু চি নিজেও অনুধাবনে সক্ষম ছিলেন। তাই তিনি গ্রেফতার হওয়ার আগেই জনগণের উদ্দেশে একটি বার্তা পাঠিয়েছিলেন। তাতে লেখা ছিল, ‘আপনারা এসব মেনে নেবেন না। রাস্তায় নামুন। সামরিক অভ্যুত্থানে দেশে আবারো স্বৈরতন্ত্র শুরু হবে।’ সু চির সর্বশেষ লিখে যাওয়া এই ছোট্ট আহ্বানটি তিনি গ্রেফতার হওয়ার পর তারই রাজনৈতিক কর্মীরা যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ করেছে। সু চির এই আহ্বান কতটা কার্যকর হবে তা বলা মুশকিল। কারণ অভ্যুত্থান ও সেনা টহলে সারা মিয়ানমারবাসী আতঙ্কিত। তারা যার যার জীবন বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। সংকটময় দিনগুলোর মোকাবিলায় অর্থের প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখে এটিএম বুথগুলোয় হামলে পড়েছেন। তাই সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে তেমন একটা প্রতিরোধ গড়ে উঠবে বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে না।
গত এক দশক ধরে নির্বাচিত সরকার দেশ পরিচালনার ভার নিলেও তা কখনোই মিয়ানমার সেনাবাহিনীর প্রভাবমুক্ত ছিল না। অং সান সু চি নামমাত্রই স্টেট কাউন্সেলর ছিলেন। তারপরও সরাসরি ক্ষমতা হাতে তুলে নেওয়ার প্রয়োজন ছিল কি? এ প্রশ্নের জবাব বর্তমান সেনাবাহিনী তাদের নিয়ন্ত্রিত টিভি চ্যানেলে বিবৃতির মাধ্যমে দিয়েছে। তাদের প্রধান দাবি হলো, বিগত সাধারণ নির্বাচনে কারচুপি ও জালিয়াতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল। বেসামরিক সরকার সে বিষয়ে কোনো পদক্ষেপই নেয়নি। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, ২০২০ সালের ৮ নভেম্বর অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে সু চির নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসি (এনএলডি) সেনাসমর্থিত ইউনিয়ন সলিডারিটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টিকে (ইউএসডিপি) পর্যুদস্ত করে ফেলে। দলটি সাবেক জেনারেল ও সেনাকর্মকর্তাদের নিয়ে গড়া। এর পর থেকেই সেনাবাহিনী নির্বাচনে কারচুপি ও জালিয়াতির অভিযোগ করে এসেছে। এবং এর মাত্রা এতটাই বেশি ছিল যে ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্টের একটি বিবৃতিতেও কারচুপির বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে জায়গা করে নেয়। ভাইস প্রেসিডেন্ট মিন্ট সয়ে সরাসরিই বলেছেন, ‘বহু দলের অংশগ্রহণে হওয়া নির্বাচনে একটি সুষ্ঠু ভোটার তালিকা প্রস্তুতে ব্যর্থ হয়েছে নির্বাচন কমিশন।’ কিন্তু নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে এমন অভিযোগের কোনো প্রমাণই দেখাতে পারেনি সেনাবাহিনী। এটা যেন মার্কিন বিদায়ী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পেরই অভিযোগের প্রতিসুর। তারপরও শাসনভার নিজেদের হাতে তুলে নেওয়ার অন্য আরও কারণ দেখছেন বিশ্লেষকরা। আসলে মিয়ানমারের সেনাবাহিনীতে নিজেদের হার মেনে নেওয়ার মতো মনোভাব তৈরি হয়নি। একটানা ৫০ বছর দেশটি শাসন করেছে সেনাবাহিনী। তারপর ২০১৫ সালে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার কেন্দ্রে না হলেও কাছাকাছি আসে সু চির নেতৃত্বাধীন বেসামরিক সরকার। ২০২০ সালে চরম বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে সেনাসমর্থিতরা। এ ঘটনা সু চির প্রতি সেনাবাহিনীর এক ধরনের স্থায়ী অনাস্থা তৈরি করে। তারা আর কালকেক্ষপণ করতে চায়নি। তাই নতুন সংসদের প্রথম অধিবেশন বসার কয়েক ঘণ্টা আগেই সু চিকে সরিয়ে দিয়ে ক্ষমতা নিজেদের হাতে তুলে নেয়। মিয়ানমারের সেনাবাহিনী নিজেদের সর্বেসর্বা হিসাবে দেখে। সেক্ষেত্রে তারা যে তাদের ন্যূনতম ঘাটতিকে মেনে নেবে না, এটি তাদের দৃষ্টিভঙ্গির ভেতরেই আছে। রোহিঙ্গা সমস্যার আগ পর্যন্ত বিশ্ব মিডিয়া অং সান সু চিকে জাতির মা হিসাবে দেখাত। এর বিপরীতে সেনাবাহিনী নিজেদের জাতির পিতা হিসাবে দেখে। এ কারণে গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের এক ধাপ উপরে তারা দেখতে চায় নিজেদের।
অং সান সু চির জীবন পর্যালোচনা করলে প্রচুর বৈপরীত্যের সন্ধান পাওয়া যাবে। তিনি সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করা মানুষ। আবার সামরিক বাহিনীর বাইরেও যেতে পারেননি। যেহেতু তার বাবা অং সান মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা, তাই তিনি বরাবরই বলে এসেছেন, এদেশের সামরিক বাহিনীর সদস্যরা আমার বাবার সন্তান।
কিন্তু তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন গণতন্ত্রের মানসকন্যা হিসাবে। মিয়ানমারে ১৯৬২ সালে সেনা অভ্যুত্থানের পর থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত আর কোনো নির্বাচন হয়নি। সু চি এই সেনাশাসনের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৮৮ সালে ৪৩ বছর বয়সে রাজনীতিতে যোগ দেন। সে বছর রাজধানীতে প্রায় ৫ লাখ মানুষের সমাবেশে বক্তৃতা করেন। তার এক মাস পরই সেনাবাহিনী তাকে গৃহবন্দি করে। কমবেশি দেড় যুগ সু চি একই বাড়িতে গৃহবন্দি অবস্থায় জীবন কাটান।
তার কারণেই বিশ্বের দৃষ্টি পড়ে মিয়ানমারের ওপর। ১৯৯০ সালে সু চি শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার পান। তখন থেকেই বিশ্বের মানুষ মিয়ানমার সম্পর্কে নতুন করে আগ্রহ দেখাতে শুরু করে। নোবেল শান্তি পুরস্কারের প্রাপ্ত অর্থ, যার পরিমাণ ১২ লাখ ডলার, তার পুরোটাই দান করে দেওয়া হয় মিয়ানমারের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে ব্যয়ের জন্যে। সে সময় থেকে সু চি রাজনীতির বাইরেও একজন মানবাধিকার কর্মী হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। কিন্তু ২০১৫ সালে ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর তিনি নিজেকে রাজনীতিক হিসাবেই প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন।
সামরিক বাহিনীর সঙ্গে সমঝোতা করে সু চি যে রাজনীতির পথে হাঁটতে শিখলেন, সেখানে মানবিক দিকটি অনেকখানিই মলিন হয়ে গিয়েছিল। তার নিজের দেশেই আরাকান রাজ্যে রোহিঙ্গাদের ওপর যে গণহত্যা চালিয়েছিল সেনাবাহিনী, তিনি তাকে সমর্থন দেওয়ার বাইরে যেতে পারেননি। বাংলাদেশে যে ১১ লাখ রোহিঙ্গা অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে জীবনযাপন করছে, তার প্রতি কোনো সুবিচারের উদ্যোগ নিতে পারেননি। সব মিলিয়ে গণতন্ত্রের মানসকন্যা হিসাবে অনেক অপ্রত্যাশিত কাজই তিনি করেছেন। তারপরও মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর এভাবে ক্ষমতা দখল কোনো গণতন্ত্রমনা মানুষ মেনে নিতে পারে না।
আমাদের পররাষ্ট্রনীতিতে সাধারণত মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রতিফলন ঘটে। আমরা সব সময়ই সব দেশের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী। আমরা কোনো দেশকে সামরিকভাবে আক্রমণের বিপরীতে আত্মরক্ষাকেই ন্যায় বলে বিবেচনা করি। আমরা কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করারও বিরোধী। কিন্তু এমন কতগুলো ইস্যু আসে যা ওই দেশের সীমানা পেরিয়ে বিশ্ব দরবারে প্রবেশ করে। তার একটি হলো জনগণের মৌলিক অধিকার। যদি কোনো দেশের শাসকগোষ্ঠী সেদেশের জনগণের ওপর দমনপীড়ন চালায় তাহলে তা বিশ্ববাসী তাকিয়ে দেখবে না। আমরা পাকিস্তানিদের দমনপীড়নের প্রতিবাদ করে এবং বিশ্ববাসীর সমর্থন নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ পেয়েছি। তাই আমরা জনমতকে গুরুত্ব দেই এবং সম্মান করি। কিন্তু এ মুহূর্তে আমাদের আন্তর্জাতিক ভাবনার বাইরেও অতিরিক্ত শঙ্কা যুক্ত হয়েছে, যা হলো-রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের ওপর এর কোনো প্রভাব পড়বে কিনা? এ নিয়ে অনেকেই তাদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। কেউ কেউ আবার মাইন্ডসেট থেকে ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তবে সব কিছু বিবেচনা করে যা দাঁড়ায় তা হলো, প্রত্যাবাসন ব্যাহত না হওয়ার ভাবনার যেমন যুক্তি আছে, আবার ব্যাহত হওয়ারও আশঙ্কা আছে।
রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে বর্তমান সামরিক অভ্যুত্থান কোনো প্রভাব ফেলবে না বলে যারা মনে করেন, তাদের কাছে উদাহরণ আছে। সাধারণত বাংলাদেশ থেকে রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেওয়ার কাজটি সম্পাদিত হবে বাংলাদেশ-মিয়ানমারের মধ্যকার চুক্তির মাধ্যমে। অর্থাৎ বিষয়টি রাষ্ট্রের, কোনো ব্যক্তির নয়। তাই ব্যক্তির অপসারণ চুক্তির অপসারণ হতে পারে না। উদাহরণ হিসাবে দেখা যায়, ’৭০ ও ’৯০-এর দশকে বাংলাদেশ থেকে একটি বড় আকারের রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন ঘটেছিল। তখন দেশটির রাষ্ট্রক্ষমতায় ছিল সামরিক বাহিনী। সে তুলনায় বিগত বেসামরিক সরকার ১১ লাখ রোহিঙ্গার মধ্য থেকে একজনকেও মিয়ানমারে নিয়ে যায়নি। এর বিপরীত মতটাও উপেক্ষা করার মতো নয়। অনেকেই মনে করেন, ২০১৭ সালে রোহিঙ্গাদের ওপর যে গণহত্যা চালানো হয়েছে এবং একটি বড় আকারের জনগোষ্ঠীকে বাংলাদেশে ঠেলে দেয়া হয়েছে তাতে সেনাবাহিনী সরাসরি জড়িত ছিল। তাছাড়া সামরিক বাহিনী রোহিঙ্গাদের সেদেশের নাগরিক হিসাবেই গণ্য করে না। সু চি এই ইস্যুতে যত নিন্দনীয়ই হন, বেসরকারি সরকার হওয়ায় আন্তর্জাতিকভাবে চাপ সৃষ্টির একটা ক্ষীণ সম্ভাবনা ছিল, যা এখন আর সম্ভব হবে না।
আমাদের সঙ্গে মিয়ানমারের মীমাংসা করার একটাই বিষয়-রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন। চীন মিয়ানমার সরকারকে সমর্থন দিচ্ছে। আমরা কূটনৈতিক প্রক্রিয়ায় রোহিঙ্গা ইস্যুতে চীনের সমর্থন আদায় করতে পারি কিনা তা-ই দেখার বিষয়।
মুঈদ রহমান : অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়


 বাঙ্গালী কণ্ঠ ডেস্ক
বাঙ্গালী কণ্ঠ ডেস্ক