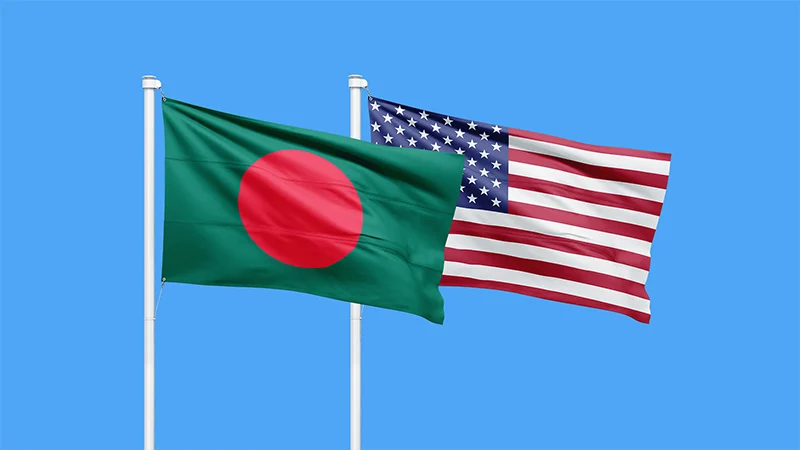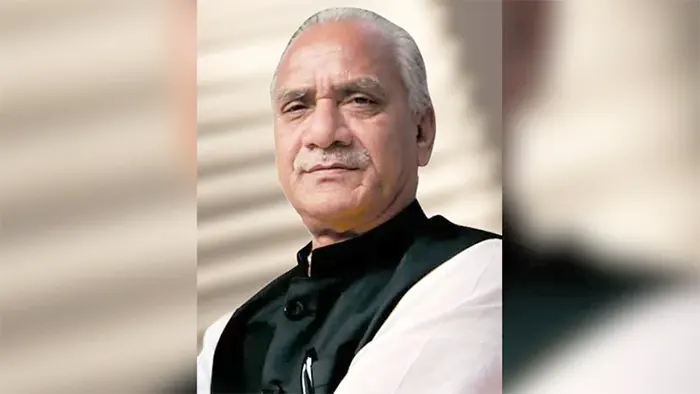যুক্তরাষ্ট্র প্রায় অর্ধশতাব্দীর বেশি সময় ধরে বিশ্বের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমরনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এ ছাড়া ১৯৯০-পরবর্তী প্রায় এক মেরুকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থায় ক্ষমতার মেরুকরণে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান এখনো প্রায় ‘অদ্বিতীয়’। এসব নানা রকম কারণে বিশ্বের বেশির ভাগ দেশ, এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলোও নিজেদের স্বার্থ সুরক্ষায় বিভিন্ন কৌশলে যুক্তরাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি, যোগাযোগ রক্ষা ও সম্প্রসারণের চেষ্টা করে থাকে।
যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ও নীতিকাঠামোতে বিদেশি রাষ্ট্র বা পক্ষগুলোর বৈধ সম্পৃক্ততার সুযোগ রাখা হয়েছে (লবিংয়ের মাধ্যমে)। এর ফলে দেখা যায়, বৃহৎ প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র চীন থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র নগররাষ্ট্র সিঙ্গাপুর বা কাতার পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের এই অভ্যন্তরীণ নীতিকাঠামোতে নিজেদের স্বার্থ সুরক্ষায় সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত থাকে।
যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যিক ও বিনিয়োগ স্বার্থ রয়েছে। আমাদের মূল রপ্তানি পণ্য রেডিমেড গার্মেন্টস বা তৈরি পোশাকের একক বৃহত্তম বাজার হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র (ব্লক হিসেবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন)। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগ, বাংলাদেশের রপ্তানি খাতের জন্য জিএসপি–সুবিধা বহাল ও সম্প্রসারণ, প্রযুক্তি স্থানান্তর, গবেষণা সহযোগিতা, গভীর সমুদ্রে সম্পদ আহরণ—এসব বিষয়ও রয়েছে।
এসব বিবেচনায় অর্থনৈতিক ও কৌশলগত স্বার্থ সুরক্ষা, রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্তন, আন্তসীমান্ত মাদক চোরাচালান ও মানব পাচার রোধ, মিয়ানমার ও ভারতীয় সীমান্তে নানামুখী হুমকি ও অস্থিরতার মতো ভূরাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য কৌশলগত মিত্র হতে পারে।
কিন্তু দুঃখজনক বাস্তবতা হচ্ছে, রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনায় সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় দূরদৃষ্টি ও কর্মকৌশল না থাকায় যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও নীতি প্রণয়ন কাঠামোয় বাংলাদেশের হয়ে কোনো পদ্ধতিগত ও সংগঠিত প্রচেষ্টা প্রায় অনুপস্থিত। এ কারণে বাংলাদেশবিরোধী নানা পক্ষ, যারা যুক্তরাষ্ট্রের নীতি প্রণয়নের জটিল প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত, তারা এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে থাকে। এ দুর্বলতা কাটানোর উপায় কী হতে পারে?
পেশাগত ও কৌশলগত নানা কারণে বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার দীর্ঘ সংগ্রামের অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর ও বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে আমার প্রায় অর্ধদশকের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। এই সম্পর্কের সূত্রে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও নীতিকাঠামোর কর্মযজ্ঞ কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে।
এই ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার আলোকে আমি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থ সুরক্ষায় রাজনীতিক ও নীতিনির্ধারকদের কীভাবে যুক্তরাষ্ট্রের জটিল নীতিকাঠামোয় বাংলাদেশ একটি শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করতে পারে, তা নিয়ে এ লেখায় কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। পাশাপাশি পদ্ধতিগতভাবে দেশের স্বার্থ সুরক্ষায় কাজে লাগতে পারে, সে রকম কিছু পরামর্শ উপস্থাপন করছি।
যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি কাঠামোয় কিছু দৃশ্যমান, কিছু অদৃশ্য ‘ক্রীড়নক’ রয়েছে; যদিও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমরা কেবল দুটি পক্ষের উপস্থিতি দেখি।
প্রথম পক্ষ হচ্ছে সরাসরি নীতিনির্ধারণে সম্পৃক্ত সরকারের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তারা। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ, প্রেসিডেন্টের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা, হোয়াইট হাউসের সিনিয়র কর্মকর্তারা এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তারা।
দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছেন স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা। প্রায় প্রতিটি দেশের জন্যই স্টেট ডিপার্টমেন্টে একটি ডেস্ক থাকে এবং সেখানে এক বা একাধিক কর্মকর্তা নিযুক্ত থাকেন। তাঁরা বিভিন্ন দেশে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসের সঙ্গে মিলে মাঠপর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ, সংকলন, বিশ্লেষণ ও মেমো তৈরির কাজ করে থাকেন।
অর্থাৎ তাঁরা একটি ‘তথ্য–লুপ’ হিসেবে কাজ করেন। এই পর্যায়ের কর্মকর্তারা নীতিনির্ধারণের জন্য তথ্য ও বিশ্লেষণ তৈরি করেন। তাঁদের সরাসরি নীতিনির্ধারণী ভূমিকা নেওয়ার সুযোগ কম। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ও কূটনৈতিক পর্যায় থেকে মূলত এই দুই স্তরের সঙ্গে সম্পৃক্ততার চেষ্টা করা হয়।
কিন্তু এই দুই স্তরের বাইরেও আরও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পক্ষ রয়েছে, যারা পররাষ্ট্র বিভাগের কৌশলগত সিদ্ধান্তে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে। এর মধ্যে প্রতিরক্ষা দপ্তর ও গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ (সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি) তার অন্যতম। যদিও প্রথম দুটি স্তরের বাইরের রাষ্ট্রের নাক গলানোর ও প্রভাবিত করার সুযোগ একেবারেই সীমিত। কিন্তু এসবের বাইরে একটি গুরুত্বপূর্ণ ‘ইকোসিস্টেম’ রয়েছে, যেটি সরকারের এসব নীতিনির্ধারণে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।
এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ‘থিঙ্কট্যাংক’। যুক্তরাষ্ট্রে সরকারের নীতিনির্ধারণে থিঙ্কট্যাংকগুলোর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি নানা দিক থেকে ইউরোপীয় চিন্তা ও কর্মধারা থেকে ভিন্ন।
ইউরোপের বেশির ভাগ দেশে সাধারণত আইন ও নীতিসংক্রান্ত বিতর্কের সূচনা হয় আমলাতন্ত্র থেকে (বাংলাদেশের অনুরূপ)। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে এই ভূমিকা মূলত পালন করে থাকে থিঙ্কট্যাংকগুলো। এর ফলে এখানে বিশ্বের সেরা থিঙ্কট্যাংকগুলোরও রাজনৈতিক অবস্থান স্পষ্ট।
উদাহরণস্বরূপ, ডেমোক্রেটিক পার্টির সঙ্গে সম্পৃক্ত জগৎখ্যাত ব্রুকিংস ইনস্টিটিউট অথবা রিপাবলিকান পার্টির সঙ্গে সম্পর্কিত আমেরিকান এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউট। র্যান্ড, হাডসন, সেন্টার ফর আমেরিকান প্রগ্রেস, হেরিটেজ ফাউন্ডেশন, ক্যাটো ইনস্টিটিউট, কার্নেগি এনডাওমেন্টসহ এ রকম গুরুত্বপূর্ণ থিঙ্কট্যাংকগুলো দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল রিপাবলিকান ও ডেমোক্রেটিক পার্টির ‘মস্তিষ্ক’ হিসেবে কাজ করে। যখন যে দল ক্ষমতায় থাকে, তাদের নীতিসংক্রান্ত বিতর্ক বিশ্লেষণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।
এই দুই চিন্তাধারার চিন্তক, বিশ্লেষক, একাডেমিক, গবেষকেরা নিজ নিজ পক্ষের থিঙ্কট্যাংকগুলোর সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে প্রক্রিয়াটিকে পরিচালনা করেন। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইকোসিস্টেম।
এই ইকোসিস্টেমের গুরুত্বের কারণে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এসব থিঙ্কট্যাংকের কাছে নিজেদের এজেন্ডা তুলে ধরতে এবং প্রচারণায় নানান কৌশল গ্রহণ করে থাকে। এর মধ্যে একটি পরিচিত কৌশল হচ্ছে, বিভিন্ন কর্মসূচির স্পনসর করা, নিজেদের গণ্ডির বিভিন্ন পণ্ডিতদের সেসব প্রতিষ্ঠানে স্পনসরকৃত কর্মসূচিতে নিয়োগ/পদায়ন করা। থিঙ্কট্যাংকগুলোও অর্থযোগের কারণে সোৎসাহে এসব কর্মকাণ্ডে সায় দিয়ে থাকে।
ভারত, চীন, রাশিয়া, সিঙ্গাপুর, কোরিয়া থেকে শুরু করে কাতার প্রভৃতি দেশের এসব কাজে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিনিয়োগ রয়েছে। এসব বিনিয়োগ কখনো রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে, কখনো রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বেসরকারি উদ্যোগে করা হয়।
বাংলাদেশের নীতিনির্ধারকেরা এই ইকোসিস্টেমটিকে পুরোপুরি বোঝার কিংবা কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছেন, এ রকমটা প্রতীয়মান হয় না। ফলে তাঁরা প্রক্রিয়াটিতে পদ্ধতিগত ও কৌশলগতভাবে সম্পৃক্ত হতে পারেননি। কিছু একাডেমিক বা গবেষক ব্যক্তিগত পর্যায়ে কোনো কোনো থিঙ্কট্যাংকে বাংলাদেশবিষয়ক ‘বিশেষজ্ঞ’ হিসেবে যৎসামান্য ভূমিকা পালন করেছেন। এগুলো বেশ বিক্ষিপ্ত ও বাংলাদেশবিরোধী নানা সংগঠিত গোষ্ঠীর অপতৎপরতা মোকাবিলায় একেবারেই যথেষ্ট নয়।
২০২৪ সালের ৫ অগাস্ট বাংলাদেশে তরুণদের নেতৃত্বে একটি অভূতপূর্ব অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছে। বাংলাদেশ এই অভাবনীয় পরিবর্তনের সুফল ঘরে তোলার জন্য সব ক্ষেত্রে আমূল সংস্কারের দাবি উঠেছে। একইভাবে আমাদের পররাষ্ট্রনীতি ও সম্পৃক্ততায় কৌশলগত চিন্তার উপস্থিতি জরুরি হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের পতিত স্বৈরশাসক ও তাঁর দেশি-বিদেশি সহচরদের সংঘবদ্ধ বাংলাদেশবিরোধী প্রচারণা এই কাজকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ ও জরুরি করে তুলেছে।
এ পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থ সুরক্ষা করতে হলে এবং সমন্বিত, সংগঠিত উপায়ে রাষ্ট্রের অনুকূলে ভূমিকা রাখতে হলে একটি রাষ্ট্রীয় কৌশল থাকা জরুরি। যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী অসংখ্য প্রবাসী পণ্ডিত, একাডেমিক, গবেষকদের একটি সমন্বিত তথ্যভান্ডার তৈরি ও সংরক্ষণ এবং আগ্রহী ও উপযুক্ত ব্যক্তিদের সুবিন্যস্ত উপায়ে রাষ্ট্রের কাজে লাগানোর সুযোগ খোঁজা যেতে পারে।
বিভিন্ন থিঙ্কট্যাংকে বাংলাদেশ স্টাডিজ (কিংবা অন্য কোনো জুতসই নামে) ‘চেয়ার’ চালু করে নির্বাচিত দেশীয় পণ্ডিতদের ওই ইকোসিস্টেমে মতামত প্রভাবিতকরণে কাজে লাগানো, প্রয়োজনীয় কর্মসূচিভিত্তিক স্পনসর করা, গবেষণা ও লেখালেখিভিত্তিক নানা ফেলোশিপ প্রদান এবং সেমিনার, সিম্পোজিয়াম প্রভৃতি স্পনসর করা কিংবা সক্রিয়ভাবে আয়োজন করা, এ বিপুল কর্মযজ্ঞের কিছু অংশ হতে পারে।
এক বা একাধিক থিঙ্কট্যাংক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ কাজগুলোর সমন্বয় ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ সম্ভব। এসবই বিপুল রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগের বিষয় ও ব্যক্তিপর্যায়ে প্রায় অসম্ভব। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থ সুরক্ষায় এসব ব্যয়কে বিনিয়োগ হিসেবে দেখা যেতে পারে। কেবল প্রথাগত দূতাবাসের দায়িত্বের মধ্যে না রেখে একটি দীর্ঘমেয়াদি সমন্বিত কর্মকৌশলের অংশ হিসেবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি বিশেষ সেল গঠনের মাধ্যমে কাজটি শুরু করা যায়।
এটি বলা বাহুল্য যে যুক্তরাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়াটি লেখায় বর্ণিত প্রক্রিয়ার চেয়েও জটিল। এখানে গোষ্ঠীস্বার্থ, ব্যবসায়িক স্বার্থ, অভ্যন্তরীণ নানা রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশ অনেক সময় নির্ধারক হয়ে ওঠে। তবে মোটাদাগে নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়ার উপর্যুক্ত ইকোসিস্টেমটি বোঝা এবং সেটিকে নিজেদের পক্ষে প্রভাবিত করার প্রচেষ্টাই হবে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বার্থ সুরক্ষার কাজ। অতীতে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু লবিস্ট ফার্ম নিয়োগের মাধ্যমে জনগণের প্রচুর অর্থ অপচয় করা হয়েছে। এর পুনরাবৃত্তি হবে দেশের দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থের পরিপন্থী।
ডোনাল্ড ট্রাম্প আবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্র একটি অভাবনীয় যুগে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। ট্রাম্পের বহুল আলোচিত ‘আমেরিকা-ফার্স্ট’ নীতিটি ‘আইসোলেশনিস্ট’ বা ‘বিচ্ছিন্নতাবাদী’। এটা যুক্তরাষ্ট্রের প্রথাগত পররাষ্ট্রনীতির সঙ্গে কিছু সাংঘর্ষিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।
যুক্তরাষ্ট্রে যদিও সরকার বদলের সঙ্গে সঙ্গে পররাষ্ট্রনীতি সাধারণত বদলায় না, কিন্তু ট্রাম্পের ঘোষিত কিছু ‘আইসোলেশনিস্ট’ নীতি যে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতিতে বড় ধরনের ঝাঁকুনি তৈরি করবে, তা ইতিমধ্যেই স্পষ্ট। যেমন ইউক্রেন যুদ্ধ, ন্যাটো, জাতিসংঘ, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা—এসব বিষয়ে ট্রাম্পের অবস্থান তাঁর পূর্বসূরিদের অবস্থানের প্রায় বিপরীত বলে মনে হচ্ছে। এর ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে, ট্রাম্পের আমলে যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশ নীতি কী হবে?
এর উত্তর জানতে হলে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতিতে বাংলাদেশের প্রথাগত অবস্থান দেখতে হবে। প্রথাগতভাবে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির ইকোসিস্টেমে বাংলাদেশ একটি ‘পেরিফেরাল’ রাষ্ট্র বা প্রান্তিক দেশ। যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বড় ধরনের স্বার্থ থাকলেও সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের বড় ধরনের কোনো অংশীদারত্ব ছিল না। তবে সাম্প্রতিক কালে এ পরিস্থিতির কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে।
২০২২ সালে মার্কিন কংগ্রেসে ‘বার্মা অ্যাক্ট’ পাসের পর এই অঞ্চল নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ আগ্রহের বিষয়টি প্রকাশ পায়। বার্মা অ্যাক্ট মূলত মিয়ানমারের সামরিক জান্তার মানবাধিকার লঙ্ঘনের জবাবদিহি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রণীত হলেও বিভিন্ন বিশ্লেষক দাবি করেন, চীন-মিয়ানমার সামুদ্রিক বাণিজ্যপথ ঘিরে এ অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের যে নতুন হিসাব-নিকাশ, এই আইন তারই প্রতিফলন।
এমনটি হলে বাংলাদেশ স্পষ্টতই যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তাসংক্রান্ত সমীকরণেরও অংশ হয়ে পড়বে। আমি মনে করি, সে ক্ষেত্রে ডোনাল্ড ট্রাম্প বাংলাদেশ বিষয়ে তার পূর্বসুরি জো বাইডেনের নীতি অব্যাহত রাখবেন এবং নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণে সচেষ্ট হবেন।
পৃথিবীর সব দেশই নিজ নিজ স্বার্থ বিবেচনায় অপর দেশের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে বা বজায় রাখে। বাংলাদেশের উচিত হবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিকাশমান নানা পরিস্থিতিকে পরিপূর্ণভাবে অনুধাবন করা, সম্ভাব্য ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা এবং সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো। ঝুঁকিকে সুযোগ ও সম্ভাবনায় রূপান্তরের চিরায়ত কৌশলটি রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে আত্মস্থ করতে হবে।
আন্তরাষ্ট্রীয় দর–কষাকষিতে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ, জিএসপি পুনর্বহাল ও পোশাক খাতকে এর অন্তর্ভুক্তকরণ, মার্কিন বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা, প্রযুক্তি স্থানান্তরে বেসরকারি খাতের সঙ্গে কাজ করা, শিক্ষা ও গবেষণা সহযোগিতার উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ, কৌশলগত জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ভূরাজনৈতিক চ্যালেঞ্জকে সুযোগে পরিণত করা—এ ধরনের কাজে মনোনিবেশ করতে হবে।
নতুন সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জকে কাজে লাগিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ কীভাবে নিজেদের দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থ হাসিল ও সুরক্ষা করতে পারবে, সেটার অনেকাংশ নির্ভর করবে বাংলাদেশের নীতিনির্ধারকদের যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি প্রণয়ন পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক বোঝাপড়া এবং সেভাবে দীর্ঘমেয়াদি কর্মকৌশল প্রণয়নের দক্ষতা ও প্রজ্ঞার ওপর।


 বাঙ্গালী কণ্ঠ ডেস্ক
বাঙ্গালী কণ্ঠ ডেস্ক