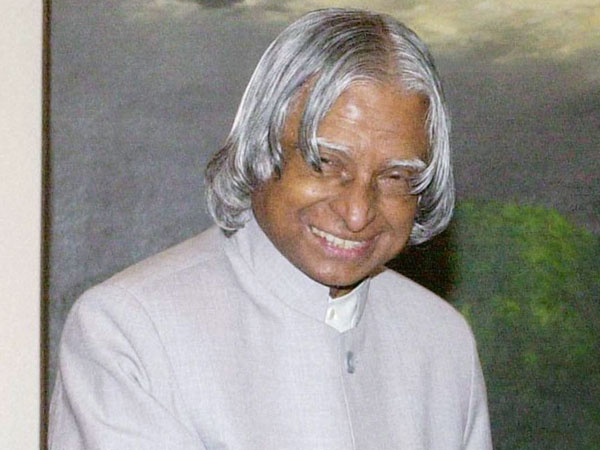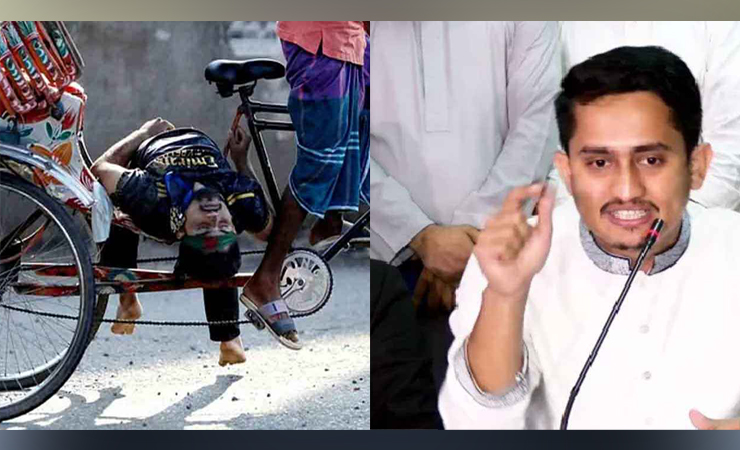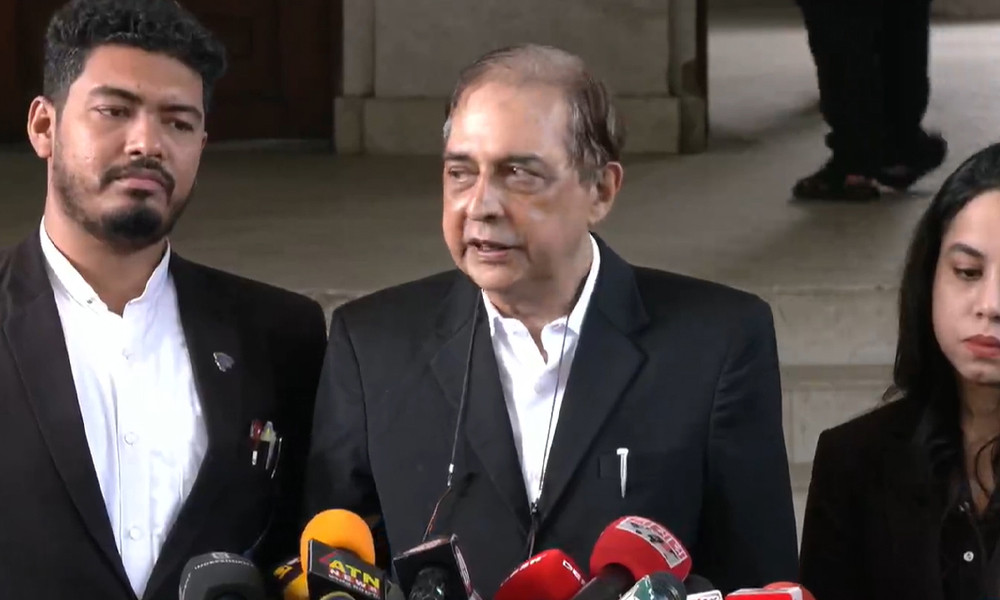জাকির হোসাইনঃ বাংলার মানুষের কাছে অনুদ্ঘাটিত অপরূপ সৌন্দর্যের বিচিত্র লীলাভূমি বাংলার রূপের রাণী হাওর যেন সাগরের ছোট বোন হয়। এখানে বর্ষার অথৈ জলে হাঁস ও মাছেরা প্রাণখোলে খেলা করে। ঢেউয়ের ভাঁজে ভাঁজে অবিরাম ছুটে চলে জেলেদের ছোট ছোট নৌকা। জলের বুকে অতন্দ্র প্রহরীর মত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা নলখাগড়া, করচ ও হিজলের বনের নয়নাভিরাম দৃশ্য অবলোকনে মনপ্রাণ জুড়িয়ে যায়। যতদূর চোখ যায় শুধু জল আর জল। হাওরের জল হতে উদীয়মান সকালের রঙিন সূর্য্য এবং সন্ধ্যায় অস্তাগমণের দৃশ্য সাগরকন্যা কুয়াকাটার সৌন্দর্য্যকেও হার মানায়। শুষ্ক মৌসুমের বিশাল সবুজ প্রান্তর যেন নিউজিল্যান্ড অস্ট্রেলিয়ার মতই সুশোভিত গো চারণ ভূমি।
‘হাওর’ শব্দটি ‘সাগর’ শব্দ থেকেই উৎপন্ন হয়েছে বলে মনে করা হয়। এখানের অধিবাসীদের বেশির ভাগই ‘স’ কে ‘হ’ উচ্চারণ করে থাকে। ফলশ্রুতিতে ‘সাগর’ থেকে ‘সায়র’ এবং ‘সায়র’ থেকে ‘হাওর’ শব্দটি এসেছে সাগরের অপভ্রংশ শব্দ হিসাবে। হাওর শব্দটির অর্থ হলো সরোবর, উপহ্রদ, বিল, বাওড়, জুড়ি, ডহর ইত্যাদি। দিক পরিবর্তনকারী মৃত নদীর প্লাবনভূমি হতে উৎপন্ন স্রোতহীন গতিহীন বিশাল জলাশয় হচ্ছে হাওর। হাওর মূলত গামলা আকৃতির বিশাল প্রান্তর। যদিও বছরের পর বছর পলিমাটি দ্বারা ভরাট হওয়ার কারণে এখন তা পিরিচের মত আকার ধারন করেছে। হাওরাঞ্চলকে ‘ভাটির দেশও’ বলা হয়।
বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদী দুটি হিমালয় হতে উৎপন্ন হয়ে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। আসামের লুসাই পাহাড় থেকে উৎপন্ন বরাক নদীটিও বাংলাদেশে প্রবেশ করে সিলেটের অমলসিদে সুরমা ও কুশিয়ারা নামে দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশে মিশেছে। এই সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলেই বাংলাদেশের বিখ্যাত হাওরগুলো অবস্থিত।
একসময় ব্রহ্মপুত্র নদীর গতিপথ মধুপুর গড়ের পূর্ব দিকে প্রবাহিত ছিল। ১৭৮৭ সালে বাংলাদেশে এক প্রলংকরী ভূমিকম্প ও প্রবল বন্যা হয়। যার ফলে ব্রহ্মপুত্র নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে মধুপুর গড়ের পশ্চিম দিকে বাঁক নেয়। এ নদীর পরিত্যাক্ত অঞ্চল এবং সুদূর অতীতে ভারতের মেঘালয় ও বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর সংঘটিত ‘ডাউকি চ্যুতির’ ফলে বসে যাওয়া এলাকাটিতে সুমেশ্বরী, যাদুকাটা, রকতি, ধামালিয়া, চলতি এবং সুরমা নদীর পলি ভরাটের ফলে এই এলাকায় বদ্ধ জলাশয়ের সৃষ্টি হয়।
দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত দেশের সাতটি জেলা জুড়ে বিস্তৃত হাওর এলাকার মোট আয়তন প্রায় ৫০০০ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা প্রায় ২ কোটি। এটিই দেশের প্রধান নিম্নভূমি। হাওরগুলোর মধ্যে সুনামগঞ্জে ১৩৩ টি, সিলেটে ৪৩ টি, হবিগঞ্জে ৩৮ টি, মৌলভীবাজারে ৪ টি, কিশোরগঞ্জে ১২২ টি, নেত্রকোনায় ৮০ টি এবং ব্রাহ্মনবাড়িয়ায় ৩ টি হাওর আছে।
বাংলাদেশের বিখ্যাত হাওরগুলো হলো শনির হাওর , হাইল হাওর, হাকালুকি হাওর, ডাকের হাওর, মাকার হাওর, টাঙ্গুয়ার হাওর, কর্চার হাওর, চন্দ্রসোনার থাল, কাওয়ার দীঘি, ডিঙ্গাপোতা, নাওটানা, চর হাইজদিয়া, লক্ষিপাশা, কীর্তনখোলা, লক্ষীপুর, গোবিন্দডোবা, চাকুয়ার হাওর ও জোয়ানশাহী ইত্যাদি।
ভ্রমণপিপাসু যে কোন মানুষ হাওরের রুপ দেখলে তার প্রেমে পড়ে যাবে। আর সে প্রেমের টানে বারবার ছুটে আসবে হাওরের বুকে। এখানে বর্ষার রূপ যেমন মোহনীয় তেমনি শীতকালে পরিযায়ী পাখিদের আগমণে হাওরাঞ্চল হয়ে উঠে সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি। প্রতিবছর নভেম্বর মাসের শুরুতেই সুদূর সাইবেরিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, চীন, মঙ্গোলিয়াসহ বিভিন্ন শীত প্রধান দেশ হতে ছুটে আসে নানান প্রজাতির রঙ বেরঙের অতিথি পাখি। বিরল প্রজাতির লালঝুঁটি, ল্যাঞ্জা হাঁস, খুন্তে হাঁস, টিকি হাঁস, পিয়াং হাঁস, ধলা বালি হাঁস, বেগুনি কালিম, পান মুরগি, সরালি, রাজ সরালি, পাতি মাছরাঙা, পাকড়া মাছরাঙা ও চখাচখির দেখা পাওয়া যায়। এছাড়াও পানকৌড়ি, ডাহুক, বালি হাঁস, গাঙচিল, বক, সারস, কাক, শক্সখচিল, পাতিকুটসহ নানা প্রজাতির দেশীয় পাখির নিয়মিত বিচরণে হাওর এলাকা যেন স্বর্গভূমিতে পরিণত হয়।
‘মাছে ভাতে বাঙালি‘ এ কথাটি আজও হাওরের মানুষদের বেলায় শতভাগ প্রযোজ্য। হাওরের মিঠা পানির মাছের স্বাদই আলাদা। কোন অতিথি একবার এ মাছ খেলে আরেকবার চাইতে লজ্জা করে না। এখানকার মাছ স্থানীয় চাহিদা মিটিয়েও দেশ-বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের শতকরা ৬ ভাগ এবং জাতীয় আয়ের শতকরা ৫ ভাগ অর্জিত হয়ে থাকে মিঠা পানির মৎস্য থেকে। হাওরের চেলাপাতা, কশিখয়রা, মলা, দাঁড়কিনা, রাণী চাঁন্দা, লাল চাঁন্দা, তিতপুুঁটি, নেফতানি, কৈ, শিং, মাগুর, টাকি, বাঘা গুতুম, বাঁশপাতা, লাঙ্গাটালু, গোলা, বালুগড়া, চাপিলা, বাউশ, গজার, পাবদা, কাঙলা, চিতল, মেনী, মধু, তারা বাইম, কাইক্কা ইত্যাদি নানা প্রজাতির মাছ ছাড়াও রিটা, বাঘাইর, নান্দিনা, জাঙ্গল, আইর, মহাশোল, টেংরা, বোয়াল, কালবাউশ উল্লেখযোগ্য। বাণিজ্যিকভাবে আধুনিক পদ্ধতিতে এখানে মাছ চাষের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।
বিশ্ব জীব-বৈচিত্রের অংশ হিসাবে ২০০০ সালের ২০ জানুয়ারি সুনামগঞ্জের টাঙ্গুয়ার হাওরকে ‘রামসার সাইট’ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। সুন্দরবনের পর এটি বাংলাদেশের দ্বিতীয় রামসার সাইট। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৭১ সালে ইরানের রামসারে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণে ‘কনভেনশন অন ওয়েটল্যান্ডস’ নামক একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষর করে। পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্রসহ ১৫৮ টি দেশ এতে স্বাক্ষর করে। টাঙ্গুয়ার হাওরে আছে ২০৮ প্রজাতির পাখি, ১৪১ প্রজাতির মাছ, ১১ প্রজাতির উভচর প্রাণি, ৩৪ প্রজাতির সরীসৃপ, ২১ প্রজাতির সাপ এবং ২০৮ প্রজাতির উদ্ভিদ।
মৎস্য সম্পদের মত হাওর অঞ্চল ধান উৎপাদনেও উদ্বৃত্ত অঞ্চল। হাওরের প্রধান শস্য ধান হলেও এখানে পাট, গম, আলু, ডাল, বাদাম, ভূট্টা, আখ, সরিষা, মটরশূটিসহ নানা প্রজাতির শাক-সবজি জন্মে। শীত ও বর্ষাকালে এখানের অনেক জমিই অনাবাদী থেকে যায়। এছাড়া এখানের বেশিরভাগ জমিতেই বছরে একটিমাত্র ফসল ফলানো হয়ে থাকে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ এবং আবহাওয়া উপযোগী বীজ আবিষ্কারের মাধ্যমে হাওরের কৃষিকে কাজে লাগিয়ে হাওর এলাকাকে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ শস্য ভান্ডারে পরিণত করা যায়। বর্ষাকালে ভাসমান পদ্ধতিতে এখানে সবজি চাষের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।
হাওরাঞ্চল খনিজ সম্পদেও সমৃদ্ধ। এখানে উন্নত মানের বালু, চুনা পাথর, নুড়ি পাথর, কয়লা, পিট কয়লা পাওয়া যায়। এছাড়ারও এখানে প্রচুর পরিমাণে প্রাকৃতিক গ্যাস এবং ইউরেনিয়ামের মজুদ রয়েছে বলে বিশেজ্ঞরা ধারনা করছেন।
বাংলাদেশে মিঠা পানির সবচেয়ে বড় উৎস হলো হাওরাঞ্চল। অদূর ভবিষ্যতে দেশে পানীয় জলের তীব্র সংকট দেখা দেওয়ার ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। আর সে সংকট মেটাতে হাওরের এই বিপুল পরিমাণ মিঠা পানিই হতে পারে একমাত্র সমাধান।
ইতিহাস ঐতিহ্যেও হাওরাঞ্চল অত্যন্ত গৌরাবান্বিত। বাংলার বার ভুঁইয়ার এক ভুঁইয়া হিসাবে পরিচিত ঈশা খাঁ ১৫৮০ সালে কোচ রাজাকে পরাজিত করে কিশোরগঞ্জের জঙ্গলবাড়ি দুর্গ দখল করে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলার মানুষ বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পরবর্তী সময়ে নিজস্ব সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়।
নদী নালা, খাল বিলে ভরপুর হাওর এলাকা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতেও সমুজ্জ্বল। এখানের মাঝি মাল্লারা নৌকার দাঁড় বাইতে বাইতে প্রাণ স্পন্দনে গেয়ে উঠে সারি গান, ভাসান গান, ভাটিয়ালি গান। শীত ও হেমন্তের পরিশ্রান্ত দিনের শেষে শুরু হত কীর্তন, জারি গান, মুর্শিদী, বাউল, ধামাইল এবং ঘাটু গানের আসর। হাসন রাজা, রাধা রমন, আব্দুল করিম, বাউল জালাল, উকিল মুন্সি এই মাটি ও মানুষেরই সন্তান। যাদের গান না হলে বাংলার সঙ্গীতাঙ্গন অপূর্ণ থেকে যায়। হাওরের কূলে বেড়ে উঠা হুমায়ুন আহমেদ, নির্মলেন্দু গুণ, হেলাল হাফিজ, মুহাম্মদ জাফর ইকবালদের পদচারণায় বর্তমান সাহিত্য জগত মুখরিত।
শ্রী চৈতন্য দেবের পিতৃভূমি ও হযরত শাহ্ জালাল, শাহ্ পরান অলি আউলিয়ার পদধূলি ধন্য হাওরাঞ্চল ধর্মীয় সম্প্রীতিতে এক শান্তির জনপদ। সাম্প্রতিক সময়ে উথ্থিত মৌলবাদীদের বিচ্ছিন্ন কিছু সহিংসতা ব্যতিত যুগ যুগ ধরে হিন্দু-মুসলিম, মন্দির-মসজিদ এবং শ্মশান- গোরস্থান পাশাপাশি অবস্থানের মধ্য দিয়ে এখানে গড়ে উঠেছে সুসংহত ধর্মীয় সম্প্রীতি। এক ধর্মের ধর্মীয় এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদিতে অন্য ধর্মের মানুষদের স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে রচিত হয়েছে ভালবাসার মেলবন্ধন যা সমগ্র বাংলাদেশের জন্যই অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।
প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর হলেও মানুষের অতীব জরুরী মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ না হওয়ায় হাওরাঞ্চলের জীবন-যাত্রার মান অত্যন্ত নিম্ন।
শিক্ষা-দীক্ষায় হাওরাঞ্চল এখনও অনেক অনগ্রসর। বৎসরের অধিকাংশ সময় পানিতে নিমজ্জিত থাকার ফলে শিশুরা নিয়মিত স্কুলে যেতে পারে না। অবকাঠামোগত অসুবিধার কারনে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেনি। এছাড়া অধিকাংশ এলাকাতেই বসত বাড়ি এবং বাসস্থানের উপযোগী জমির অভাব, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ও প্রযুক্তিগত সুবিধা না থাকায় শিক্ষকরাও হাওরাঞ্চলে পড়াতে আগ্রহী হয় না। হাওরাঞ্চলে শিক্ষার সম্প্রসারে সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। যেমন: বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকের ’শিক্ষাতরীর‘ কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এছাড়া শিক্ষকদেরকেও বিশেষ সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে হাওরে শিক্ষা দানে উৎসাহিত করা দরকার।
এ এলাকার চিকিৎসা ব্যবস্থা অত্যন্ত নাজুক। উপজেলা পর্যায়ে একটি করে হাসপাতাল থাকলেও ভাল ডাক্তার এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের অভাবে হাওরবাসী চিকিৎসা সুবিধা থেকে বঞ্চিত। প্রাচীন যোগাযোগ ব্যবস্থার কারনে জরুরী কোন রোগীকে যথাসময়ে হাসপাতালে পৌছানো সম্ভব হয় না। ফলে অনেক রোগীকেই চিকিৎসা সেবাহীনভাবেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হয়। প্রসূতি মাতা এবং শিশু মৃত্যুর হার এখানে অন্যান্য এলাকার চেয়ে অনেক বেশি। হাওরাঞ্চলে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের হার মাত্র ৩৫ শতাংশ। ফলে যত্রযত্র মল-মূত্র ত্যাগ করায় ডায়রিয়া, আমাশয়, জন্ডিস ইত্যাদি রোগে প্রতি বছর অনেক লোক মারা যায়। এছাড়া ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবও এখানে অনেক বেশি।
হাওরাঞ্চলের প্রধান সমস্যা হলো যোগাযোগ ব্যবস্থাা। বর্ষার জলে ভাসা দ্বীপের মত গ্রামগুলোতে নৌকা ও ট্রলার ছাড়া যোগাযোগের আর কোন ব্যবস্থা নেই। হেমন্তে পায়ে হেঁটে এক এলাকা থেকে আরেক এলাকায় যাতায়াত করতে হয়। হাওরের যোগাযোগ ব্যবস্থা নিয়ে স্থানীয় একটি স্বার্থক প্রবাদ আছে, “ বর্ষায় নাও, হেমন্তে পাও।” এই হলো এখানকার বাস্তবচিত্র। হাওরবাসীর পশ্চাদপদতার পিছনে মূলত এই প্রাচীন যোগাযোগ ব্যবস্থা। হাওরের জেলাগুলোকে কেন্দ্র করে অন্যান্য জেলাগুলোর সাথে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারলে এখানের মানুষের জীবন-যাত্রার মানের যেমন পরিবর্তন সাধিত হবে তেমনি এই এলাকার উদ্বৃত্ত মাছ ও খাদ্য শস্য দেশের নানা প্রান্তে সহজে রপ্তানি করা যাবে। পাশাপাশি বাংলাদেশের পর্যটন ও ব্যবসা-বাণিজ্যে একটি নতুন যুগের সূচনা হবে। এ জন্য প্রয়োজন সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ের সকল মহলের সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা।
এক সময় হাওরের জমি, জল, ফসল ও মাছের মালিকানা হাওরবাসীর থাকলেও ইংরেজ শাসন আমলে চিরস্থায়ী বন্দোবরেস্তর কারণে প্রথমে জমিদার এবং পরবর্তিতে পাকিস্তান সরকারের আমলে চালু হওয়া ইজারা প্রথার কারণে ইজারাদাররা মাছের মালিক হয়। কমরেড বরুন রায়, আলফাত, মুক্তার এদের নেতৃত্বে হাওরবাসী মাছের মালিকানা ফিরে পেতে ‘জল যার জলা তার’ শ্লোগান নিয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ ‘ভাসানপানির আন্দোলন’ নামে অনেক আন্দোলন সংগ্রাম এবং রক্ত ঝরালেও আজও তারা মাছের মালিকানা ফিরে পায় নি। সরকারের উর্ধ্বতন মহলের নেক নজর না পেলে ইজারা প্রথা বিলুপসাধন সম্ভব নয়। জোতদারদের কাছ থেকে সাধারণ জেলেদেরকে মাছের মালিকানা ফিরিয়ে দিলে হাওরের দারিদ্র মোচন একেবারে সহজ হয়ে যাবে।
হাওর এলাকার উন্নয়নের জন্য সরকার কর্তৃক ২০০০ সালে হাওর ও জলাভূমি উন্নয়নবোর্ড পুনঃগঠিত গঠিত হলেও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা এবং অর্থ বরাদ্দের অভাবে তা এখনও খুড়িয়ে খুড়িয়ে চলছে। জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থে অত্র প্রতিষ্ঠানটিকে সচল করার মধ্য দিয়ে হাওর উন্নয়নে মহাপরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করা দরকার।


 বাঙ্গালী কণ্ঠ ডেস্ক
বাঙ্গালী কণ্ঠ ডেস্ক